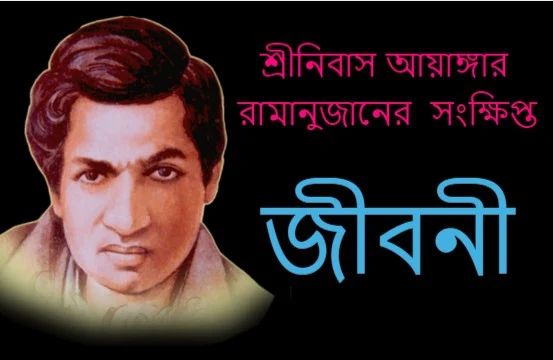সত্যজিৎ রায়ের জীবনী ।। সাল অনুযায়ী সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জী ।। কত বছর বয়সে ফেলুদা লেখা শুরু করেন ? জেনে নিন
সত্যজিৎ রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী
"পথের পাঁচালীর তুল্য ছবি বিশ্বে এ যাবৎ নির্মিত হয়নি।"
সত্যজিৎ রায় যে বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকদের একজন, এ ব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশের অবকাশ কম। তিনি সামগ্রিকভাবে বাঙ্গালী জাতিকে বিশ্বের দরবারে গৌরবান্বিত করেছেন। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে দুনিয়ার সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম চিত্রপরিচালক আইজেনস্টাইনের স্ত্রী ও সহকারিণী মেরী সিটন কলকাতায় এসে বলেন, “পথের পাঁচালীর তুল্য ছবি বিশ্বে এ যাবৎ নির্মিত হয়নি। "
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং কলকাতায় এসে সত্যজিৎ রায়কে তাদের দেশের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করে যান। চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে সত্যজিৎ যতবার যতভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন, তার দ্বিতীয় নিদর্শন এ দেশে নেই।
জন্মঃ ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ২রা মে সত্যজিৎ রায়ের জন্ম কলকাতার এক সুপরিচিত সাংস্কৃতিক পরিবারে। তার বাবা সুকুমার রায় বাংলা সাহিত্যের এক দিকপাল কবি-লেখক। তাঁর ঠাকুরদা উপেন্দ্রকিশাের রায়চৌধুরিও একজন স্বনামধন্য শিশুসাহিত্যিক। মা সুপ্রভা রায় একজন শিক্ষিকা। সত্যজিৎ মাত্র আড়াই বছর বয়সে পিতৃহারা হন।
পড়াশুনাঃ সত্যজিৎ রায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক।কম বয়সেই ফটোগ্রাফিতে চমৎকার হাত। এর জন্য এক প্রতিযােগিতায় তিনি পুরস্কৃতও হন। শান্তিনিকেতনে তিনি যখন চিত্রশিল্পের ছাত্র, রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত। রবিঠাকুরের স্নেহধন্য হয়েছিলেন তিনি।
চিত্রাঙ্কনে ডিপ্লোমা পাবার পর সত্যজিৎ সে সময়ের বিখ্যাত বাংলা প্রকাশন সংস্থা সিগনেট প্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। সিগনেট থেকে প্রকাশিত প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের গ্রন্থের প্রচ্ছদ আঁকাই তখন তার কাজ। সেই সময় তিনি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’ পাঠ করেন ও গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর মনে বাসনা জাগে উপন্যাসটির চলচ্চিত্রায়ন করবার।
১৯৫০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় তার সঙ্গে পরিচয় হয় এখানে আউটডাের শুটিং করতে আসা বিশ্বখ্যাত ফরাসী চিত্রপরিচালক জাঁ রেনােয়ার সঙ্গে । কথা বলে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন।
কাজঃ ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সত্যজিৎ ডি, জে, কিমার কোম্পানিতে আর্ট ডিরেক্টরের চাকরি নেন ও সেই সুবাদে ইংল্যান্ডে যান। বিলেতে গিয়ে প্রচুর বিখ্যাত সিনেমা দেখেন। তাঁর চিত্রপরিচালক হবার স্বপ্ন আরও ঘনীভূত হয়। দেশে ফিরে ‘পথের পাঁচালী’-র সচিত্র চিত্রনাট্য রচনা করেন। কিন্তু সিনেমা বানাতে গেলে যে পরিমাণ টাকার দরকার, সত্যজিতের তা ছিল না। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিকল্পনার কথা জানান ও সরকারি সাহায্য প্রার্থনা করেন। নব বাংলার রূপকার বিধানচন্দ্র রায় তাকে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দেন।
সত্যজিৎ নিজের যতটুকু সম্বল ছিল, সবই ব্যয় করলেন সেই ছবি তৈরি করতে। তারপর এল সরকারি সাহায্য। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষের দিকে ‘পথের পাঁচালী’ নির্মিত হল। প্রথম প্রদর্শনের পর বাংলার শিক্ষিত জনগােষ্ঠী সত্যজিৎকে বিপুলভাবে অভিনন্দন জানান। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে কান চলচ্চিত্র উৎসবে ‘পথের পাঁচালী’ পুরস্কৃত হয় ‘শ্রেষ্ঠ মানবিক আবেদনসমৃদ্ধ চলচিত্র’ রূপে।শুরু হয়ে গেল সত্যজিৎ রায়ের জয়যাত্রা।
‘পথের পাঁচালী’-র পর একে একে তার পরিচালনায় বেরিয়ে এল ‘অপরাজিত’ ‘অপুর সংসার’ ‘জলসাঘর’ ‘পরশপাথর’ ‘তিন কন্যা’ ‘মহানগর’ ‘অশনি সংকেত’ ‘নায়ক’ ‘অভিযান’ ‘গণশত্রু’ ‘সােনার কেল্লা' , 'শতরঞ্জ কা খিলাড়ি' , 'শাখা-প্রশাখা’ ‘গুপি গায়েন বাঘা বায়েন’ ‘আগন্তুক’-এর মত ছবি। বেশির ভাগ ছবিরই তিনি একাধারে পরিচালক, চিত্র নাট্যকার ও সঙ্গীত পরিচালক। ‘অপরাজিত’ ছবি ভেনিস থেকে নিয়ে এল ‘গােল্ডেন লায়ন' ।
সত্যজিৎ একজন কুশলী সাহিত্যিকও। ফেলুদা’ ও ‘প্রফেসর শঙ্কু' তার সৃষ্টি দুটি অনবদ্য বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্র। তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থ আজও খুব পাঠকপ্রিয়। সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে রবীন্দ্রনাথের ওপর একটি অসাধারণ তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেন—যেখানে ভাষ্যকারের ভূমিকা তিনি স্বয়ং পালন করেন।
তিনি সারা বিশ্ব থেকে এত পুরস্কার পান যে তার তালিকা করতে বসলে অবাক হতে হয়। মৃত্যুর পূর্বে তার সমগ্র কীর্তির জন্য সত্যজিৎকে ‘অস্কার’ পুরস্কারও দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ সম্মান ‘ভারতরত্ন’ও তিনি লাভ করেন।
১৯৯২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল বাংলার এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা পরলােকের পথে যাত্রা করেন।
সত্যজিৎ রায়ের জীবনপঞ্জী
• ১৯২১- উত্তর কলকাতার গড়পার রােডে ২ মে (১৮ বৈশাখ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ) জন্ম হয়েছিল সুকুমার ও সুপ্রভা রায়ের ছেলে সত্যজিতের।
• ১৯২৩-১০ সেপ্টেম্বর কালাজ্বরে ভুগে মৃত্যু হল ‘আবােলতাবােল’, ‘হযবরল, ‘ঝালাপালা'র স্রষ্টা সুকুমার রায়ের,মাত্র ৩৬ বছর বয়সে।
• ১৯২৬- সুপ্রভাদেবী বালক সত্যজিৎকে নিয়ে ভবানীপুরে ভাই প্রশান্তকুমার দাসের বাড়ি উঠে আসেন।
• ১৯৩০- সাড়ে আট বছর বয়সে বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন সত্যজিৎ।
• ১৯৩৬- উপহার পাওয়া ক্যামেরায় ফোটো তুলে বিলেতের ‘বয়েজ ওন পেপার’ পত্রিকায় প্রথম পুরস্কার পান। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করে অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।
• ১৯৪০-বি এ পাশ করার পর ১৩ জুলাই ভর্তি হয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। ২০ নভেম্বর সত্যজিতের আঁকা প্রথম প্রচ্ছদ ‘পাগলা দাশু’ প্রকাশিত হয়।
• ১৯৪১- প্রথম লেখা ইংরেজি গল্প ‘অ্যাবস্ট্রাকশন’ প্রকাশিত হয় ‘অমৃতবাজার পত্রিকায়, ১৮ মে তারিখে।
• ১৯৪২- কলকাতায় জাপানি বিমান আক্রমণ। মায়ের জন্য চিন্তায় ডিসেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনের পাঠ অসমাপ্ত রেখে কলকাতায় ফেরেন। ‘অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় ইংরেজি গল্প শেডস অফ গ্রে’, ২২ মার্চ তারিখে।
• ১৯৪৩- দিলীপকুমার গুপ্ত যিনি ‘ডি কে' নামেই বেশি পরিচিত কলকাতার সাংস্কৃতিক মহলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। এর পর থেকে ডি কে-র সিগনেট প্রেসের জন্য ছবি আঁকা শুরু। এপ্রিল মাসে বিজ্ঞাপন সংস্থা ‘ডি জে কিমার’-এ ভিসুয়ালাইজার পদে যােগদান। মৌচাক’ পত্রিকায় সত্যজিতের আঁকা প্রথম ইলাস্ট্রেশন প্রকাশিত হয়।
• ১৯৪৪- চিত্রনাট্য লেখার অভ্যেস শুরু।
• ১৯৪৫- সিগনেট প্রেসের জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ‘পথের পাঁচালী’র সংক্ষিপ্ত কিশাের সংস্করণ ‘আম আঁটির ভেঁপুর। ইলাস্ট্রেশন করেন। তখনই বইটি নিয়ে ছবি করার ভাবনা আসে ।
• ১৯৪৭- হরিসাধন দাশগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, রাম হালথার, তাঁর মনে।বংশী চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে ৫ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা করলেন ‘ক্যালকাটা ফিল্ম সােসাইটি।
• ১৯৪৮-চলচ্চিত্রসংক্রান্ত প্রথম লেখা ‘হােয়াট ইজ রং উইথ ইন্ডিয়ান ফিল্মস' প্রকাশিত হয় দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায়। পারিবারিক দুটো ঘটনা উল্লেখযােগ্য। মাকে নিয়ে লেক অ্যাভিনিউতে চলে আসেন মামার বাড়ি ছেড়ে। মাধুরী ও চারুচন্দ্র দাশগুপ্তর কন্যা বিজয়ার সঙ্গে রেজিষ্ট্ৰিমতে বিয়ে হয় মুম্বইয়ে।
• ১৯৫০-‘দ্য রিভার' ছবির জন্য কলকাতায় আসেন বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি চিত্রপরিচালক জাঁ রেনােয়া। তিনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী পিয়ের-আগুস্ত রেনােয়ার পুত্রও বটে। তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচয় হয় সত্যজিতের। তাঁর লেখা ‘রেনােয়া ইন ক্যালকাটা’ প্রকাশিত হয় ব্রিটিশ পত্রিকা ‘সিকোয়েন্স’-এ। ডি জে কিমারের আর্ট ডিরেক্টর হন। ছ'মাসের জন্য বিদেশযাত্রা। অসংখ্য প্রদর্শনী, থিয়েটার, ফিল্ম। দেখে ও গান শুনে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ফিরে এসে মতানৈক্যে ডি জে কিমার ত্যাগ ও বেনসনস এজেন্সিতে যােগদান। ফিরে আসার পথে ‘পথের পাঁচালী'র চিত্রনাট্যের খসড়া। আন্তর্জাতিক মুদ্রণ প্রদর্শনীতে ‘খাই খাই’ ও ‘অনন্যা বইয়ের প্রচ্ছদের জন্য পুরস্কার অর্জন।
• ১৯৫২ অক্টোবর মাস থেকে ‘পথের পাঁচালী’র দৃশ্যগ্রহণ শুরু করেন।
• ১৯৫৩- ৮ সেপ্টেম্বর একমাত্র পুত্র সন্দীপ রায়ের জন্ম।
• ১৯৫৪- চলচ্চিত্রায়নে আর্থিক বাধার মুখােমুখি। পশ্চিমবঙ্গের সেইসময়কার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের হস্তক্ষেপে 'পথের পাঁচালী’ প্রযােজনায় এগিয়ে আসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
• ১৯৫৫- এপ্রিল মাসে নিউ ইয়র্কে মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট-এ ‘পথের পাঁচালী'র প্রথম প্রদর্শন। ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে বাংলাদেশের তরুণ সাহিত্যিক ও শিল্পীরা (ছিলেন পূর্ণেন্দু পত্রী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ) সত্যজিৎ রায় এবং কলাকুশলীদের সংবর্ধনা জানান।
• ১৯৫৬- কান চলচ্চিত্র উৎসবে ‘পথের পাঁচালী’ ‘সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক আবেদনসম্পন্ন চলচ্চিত্র হিসেবে সম্মানিত হয়। ১১ অক্টোবর মুক্তি পায় ‘অপরাজিত।
• ১৯৫৭- ভেনিসের চলচ্চিত্র উৎসবে ‘অপরাজিত’ সেখানকার সেরা পুরস্কার ‘গােল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক’ পায়। এবছরই সুকুমার রায় এথেনিয়াম ইনস্টিটিউশন কলকাতার ইডেন উদ্যানে সত্যজিৎ রায়কে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
• ১৯৫৮- পরশুরামের কাহিনিনির্ভর ‘পরশপাথর' ছবিটি ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে নির্মিত 'জলসাঘর’ও এবছরই মুক্তি পায়।
• ১৯৫৯- সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার পান। পদ্মশ্রীও পান এই বছরই। মুক্তি পায় ‘অপুট্রিলজি’র শেষ ছবি ‘অপুর সংসার'। ক্যামেরায় চোখ রেখে স্ত্রী
• ১৯৬০-১৯ ফেব্রুয়ারি প্রভাতকুমার মুখােপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে ‘দেবী’ মুক্তি পায়। নভেম্বরে মায়ের মৃত্যু।
• ১৯৬১- সুভাষ মুখােপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পাদনায় ‘সন্দেশ পত্রিকা নতুন করে প্রকাশ। বাংলায়। সাহিত্যরচনা শুরু। প্রথম রচনা এডওয়ার্ড লিয়রের ছড়া অবলম্বনে ‘পাপাঙ্গুল'-- 'তারা ছাঁকনি চড়ে সাগর পাড়ি দেবে দেবেই দেবে।..নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল পাপাঙ্গুল’। এ বছরই সন্দেশে প্রথম শঙ্কুর গল্প ‘ব্যোমযাত্রীর ডায়রি’ প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষে মুক্তি পায় তাঁর লেখা তিনটি ছােটগল্প অবলম্বনে ছবি ‘তিনকন্যা।
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সুরারােপিত তথ্যচিত্র ‘রবীন্দ্রনাথ’ও এবছর তৈরি।
• ১৯৬২- ১১ মে মুক্তি পায় প্রথম রঙিন ছবি 'কাঞ্চনজঙ্ঘা”। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে তৈরি ‘অভিযান’ ছবিটিও এবছরে সেপ্টেম্বরে মানুষ দেখতে যায় চলচ্চিত্রঘরে।
• ১৯৬৩- ‘টাইম’ পত্রিকার মতে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১১জন চিত্রপরিচালকের মধ্যে অন্যতমর শিরােপা পান। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘অবতরণিকা' ছােটগল্প অবলম্বনে ‘মহানগর’ ছবিটি মুক্তি পায়।
• ১৯৬৪- রবীন্দ্রনাথের ‘নষ্টনীড়' অবলম্বনে ‘চারুলতা’র মুক্তি। দুই অসম অবস্থানের শিশুকে নিয়ে দূরদর্শন চিত্র ‘টু’র মুক্তিলাভ। বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে ‘মহানগর’জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালকের ‘রৌপ্য ভল্লুক'।
• ১৯৬৫- যথাক্রমে প্রেমেন্দ্র মিত্রের। ‘জনৈক কাপুরুষের কাহিনী ও পরশুরামের ‘বিরিঞ্চিবাবা’ গল্প নিয়ে ‘কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' ছবির মুক্তি। পদ্মভূষণ প্রাপ্তি। প্রথম ‘ফেলুদা’ সিরিজের গল্প ‘ফেলুদার গােয়েন্দাগিরি’ প্রকাশিত ‘সন্দেশ' পত্রিকায়।
• ১৯৬৬- উত্তমকুমার অভিনীত সত্যজিৎ রায়ের নিজের কাহিনি নিয়ে তৈরি ‘নায়ক’ মুক্তি পায়।
• ১৯৬৭- শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গােয়েন্দা ব্যোমকেশকে নিয়ে চিড়িয়াখানা’ ছবি হলে মুক্তি পায়। ম্যাগসাইসাই’ পুরস্কারে সম্মানিত। বছরের শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যের বইয়ের জন্য ‘প্রােফেসর শঙ্কু’ মনােনীত হয় ‘আকাদেমি সােনার কেল্লা ছবির
• ১৯৬৯- ৮ মে মুক্তি পেল 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'। সেপ্টেম্বর মাসেই প্রথম ফেলুদার বই ‘বাদশাহী আংটি’ প্রকাশ পায়। বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক পিসি সুখলতা রাও মারা যান।
• ১৯৭০- মুক্তি পায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস নিয়ে তৈরি ছবি ‘অরণ্যের দিনরাত্রি'। প্রকাশিত হয় ‘প্রােফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা',
প্রথম গল্পসংকলন ‘একডজন গপ্পো’। সঙ্গে সুকুমার রায়ের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ “ননসেন্স রাইমস'। বছরের শেষের দিকে মুক্তি পায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়েরই কাহিনি-অবলম্বনে পুরস্কারের জন্য।
প্রতিদ্বন্দ্বী’ ছবি।
• ১৯৭১- সাহিত্যকৃতির জন্য আনন্দ পুরস্কার' লাভ। প্রকাশিত হয় ‘গ্যাংটকে গন্ডগােল’ ও ‘সােনার কেল্লা'।'রে রােমান টাইপােগ্রাফির জন্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার। “সীমাবদ্ধ' ও তথ্যচিত্র ‘সিকিম’ও এবছরই মুক্তি পায়।
• ১৯৭৩- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-অবলম্বনে ‘অশনি সংকেত' মুক্তি পায়। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘ডক্টর অফ লেটার্স’ পান। বাক্স রহস্য’ বইটি ও তাঁর সম্পাদিত বই ‘সুকুমার সাহিত্য সমগ্র'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় এবছর।
• ১৯৭৪- ২৭ ডিসেম্বর ‘সােনার কেল্লা’ ছবি হলে মুক্তি পায়।এবছর এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত হয় তাঁর। ‘কৈলাসে কেলেঙ্কারি’, ‘সাবাস প্রােফেসর শঙ্কু’ বই হয়ে বেরয়। এবছরের নভেম্বরে তাঁর আর-এক পিসি পুণ্যলতা চক্রবর্তীর অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও কামু মুখােপাধ্যায়ের সঙ্গে সত্যজিৎ মৃত্যু হয়। ইনিও ছােটদের জন্য সরস ও রম্য লেখা লিখেছেন। শান্তিনিকেতনে সত্যজিৎ রায়ের শিল্পগুরু বিনােদবিহারী
মুখােপাধ্যায়কে নিয়ে তথ্যচিত্র 'ইনার-আই' নির্মাণ।
• ১৯৭৫- ব্রিটিশ ফেডারেশন অফ ফিল্ম সােসাইটি তাঁকে ‘বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক'-এর সম্মান দেয়। প্রকাশিত হয় রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য’ ও সম্পাদিত 'সুকুমার সাহিত্য সমগ্র’র দ্বিতীয় খণ্ড।
• ১৯৭৬- ‘পদ্মবিভূষণ’ লাভ। “জয় বাবা ফেলুনাথ’, ‘আরাে এক ডজন’, ‘ফটিকচাঁদ’ প্রকাশ। এছাড়া ছাপার অক্ষরে মুক্তি পায় চলচ্চিত্রবিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন ‘বিষয় চলচ্চিত্র, ইংরেজি বই ‘আওয়ার ফিল্মস, দেয়ার ফিল্মস। সাহিত্যিক ছবির শুটিংয়ে শংকরের কাহিনি অবলম্বনে ‘জন-অরণ্য ও দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যশিল্পী বালা সরস্বতীকে নিয়ে ‘বালা’ তথ্যচিত্রও এবছরেই মুক্তি পায়।
• ১৯৭৭- ‘ফেলুদা অ্যান্ড কোং' (বােম্বাইয়ের বােম্বেটে, গোঁসাইপুর সরগরম), ‘মহাসঙ্কটে শঙ্কুর প্রকাশ।
• ১৯৭৮- মুন্সী প্রেমচন্দর গল্প নিয়ে তৈরি ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’-র মুক্তি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি লিট উপাধি প্রাপ্তি। বিশ্বভারতী থেকে 'দেশিকোত্তম' সম্মান। চার্লি চ্যাপলিন ও ইঙ্গমার বার্গম্যানের সঙ্গে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি থেকে সর্বকালের তিনজন সেরা পরিচালক’-এর সম্মানলাভ।
• ১৯৭৯- ‘গােরস্থানে সাবধান’, ‘একেই বলে শুটিং’ প্রকাশিত হয়। জানুয়ারিতেই মুক্তি পায় 'পাঁচ ভাই একসাথ মারছে ঘুসি খাচ্ছে ভাত'...আর নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা নেই। অর্থাৎ ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’। এবছর সম্মান আসে মস্কো থেকে। বিংশ শতাব্দীর সেরা ন’জন পরিচালকের অন্যতম হওয়ার সম্মান।
• ১৯৮০- ‘হীরক রাজার দেশে মুক্তি পেল। স্বয়ং প্রােফেসর শঙ্কু প্রকাশিত হল। ধানের শিষের শিশিরবিন্দুর দিকে ভারতীয় জনগণের নজর পড়ল। যাদবপুর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সত্যজিৎকে এবছর ডি লিট উপাধি দিল।
• ১৯৮১- ‘ছিন্নমস্তার অভিশাপ’, ‘হত্যাপুরী’, ‘আরাে বারাে’ বইয়ের সঙ্গে প্রকাশিত হল সম্পাদিত বই ‘সেরা সন্দেশ: ১৩৬৮৮৭। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট প্রদান। এছাড়া শিশিরকুমার সাহিত্য পুরস্কার পেলেন সত্যজিৎ রায়। শুটিংয়ের মজার অভিজ্ঞতা নিয়ে একেই বলে শুটিং’-এর জন্য ‘ফটিক স্মৃতি পুরস্কার। নিউ ইয়র্কে ‘মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট’-এ ‘ ফিল্ম ইন্ডিয়া’ উৎসবের প্রথম পর্যায়ে তাঁর এযাবৎ সব ছবির প্রদর্শনী হয়।
•১৯৮২- ফরাসি টেলিভিশন প্রযােজিত ‘পিকু’ ছবি করলেন। ছবিটির কেন্দ্রে একটি বাচ্চা থাকলেও ছবিটি বড়দের জন্যই তৈরি। ২৫ এপ্রিল ভারতীয় দূরদর্শন প্রযােজিত ‘সদগতি’ প্রদর্শনের মাধ্যমে দূরদর্শনের রঙিন ছবি সম্প্রচার শুরু। ফেলুদাকাহিনি ‘যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে' প্রকাশিত হয়। শিশুসাহিত্যিক অসামান্য অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিদ্যাসাগর ‘হীরক রাজার দেশে' ছবিতে গুপী গাইন ও বাঘা বাইন পুরস্কার দেয় তাঁকে। এছাড়াও বিদেশের অসংখ্য পুরস্কারলাভ। রােম চলচ্চিত্র উৎসবে ‘ভিসকোন্তি পুরস্কার', কান চলচ্চিত্র উৎসব।কমিটি দেয় ‘হেডলেস এঞ্জেল ট্রোফি’, ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ‘গােল্ডেন লায়ন অফ সেন্ট মার্ক' পুরস্কার পান এই আকাশচারী মানুষটি।
• ১৯৮৩- 'টিনটোরেটোর যীশু’, ‘শঙ্কু একাই ১০০' প্রকাশ পায়। ১ অক্টোবর হৃদরােগে আক্রান্ত হন তিনি।
• ১৯৮৫-‘ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু’ (নেপােলিয়নের চিঠি', এবার কাণ্ড কেদারনাথে’), “তারিণীখুড়াের কীর্তিকলাপ’, ‘মােল্লা নাসিরুদ্দীনের গল্প’ ও ‘দ্য অপু ট্রিলজি’ চিত্রনাট্য প্রকাশ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট প্রদান, দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার লাভ।
• ১৯৮৬- ওইদিকে দেখাে দেখি তাকিয়ে বিদঘুটে রাক্ষস নাকি এ/আরে না না এ যে হরু হয়েছে সে এত সরু মামা তার রাখে। তারে পাকিয়ে...সত্যজিতের নিজের লেখা ছড়া, লুইস ক্যারল,এডওয়ার্ড লিয়র প্রমুখর কবিতার অনুবাদ নিয়ে বই ‘তােড়ায় বাঁধা ঘােড়ার ডিম’ প্রকাশিত হয়।
• ১৯৮৭-আড়াই বছর বয়সে হারানাে বাবাকে নিয়ে তথ্যচিত্র করলেন 'সুকুমার রায়'। ফেলুদার বই ‘দার্জিলিং জমজমাট, ছােটদের আশ্চর্য রূপকথার বই 'সুজন হরবােলা’, কোনান ডয়েল,আর্থার সি ক্লার্ক, রে ব্র্যাডবেরির গল্পের অনুবাদ-বই ‘ব্রেজিলের কালাে বাঘ ও অন্যান্য প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ‘ডি লিট’ দিল। রাশিয়ার ‘ডুসানডে' শহরে ‘সত্যজিৎ রায় ফিল্ম সােসাইটি' উদ্বোধন।
• ১৯৮৯- ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মিতের কলকাতায় এসে লিজিয়ন অফ অনার দেন। ১৯৯১-‘আগন্তুক’ ছবি মুক্তি পায়। বিভিন্ন দেশ থেকে
সম্মানস্রোত অব্যাহত। যেমন একটি, বেলজিয়াম থেকে ‘সত্যজিৎ রায় অ্যাট সেভেন্টি' শ্রদ্ধার্ঘ্য-গ্রন্থ প্রকাশ।
• ১৯৯২- ভারতরত্ন পেলেন। ৩০ মার্চ ‘লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট'-এর জন্য অস্কারলাভ। ২৩ এপ্রিল সন্ধে ৫:৪৫কলকাতার বেলভিউ নার্সিংহােমে তাঁর মৃত্যু। অবশ্য খাতায় কলমে। আমরা জানি, তাঁর মৃত্যু নেই। হতে পারে না কখনও।
 Reviewed by Wisdom Apps
on
October 22, 2021
Rating:
Reviewed by Wisdom Apps
on
October 22, 2021
Rating: